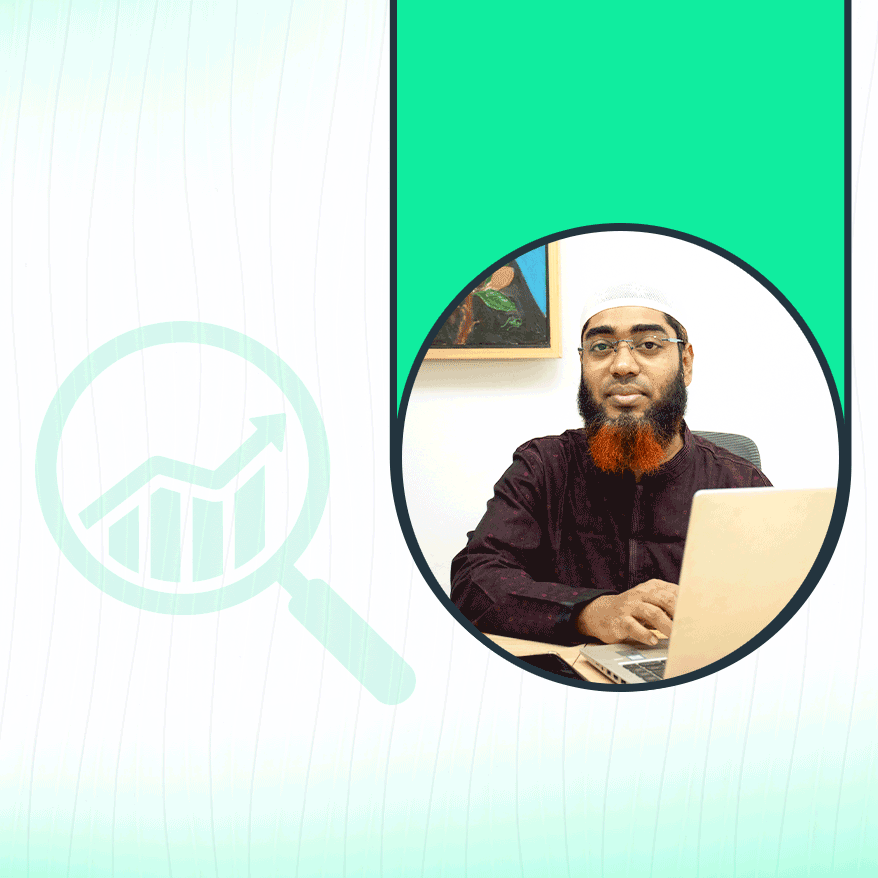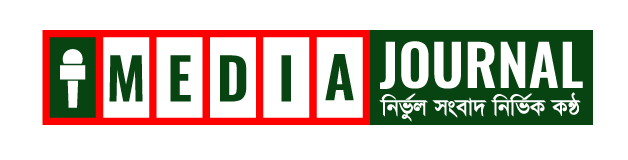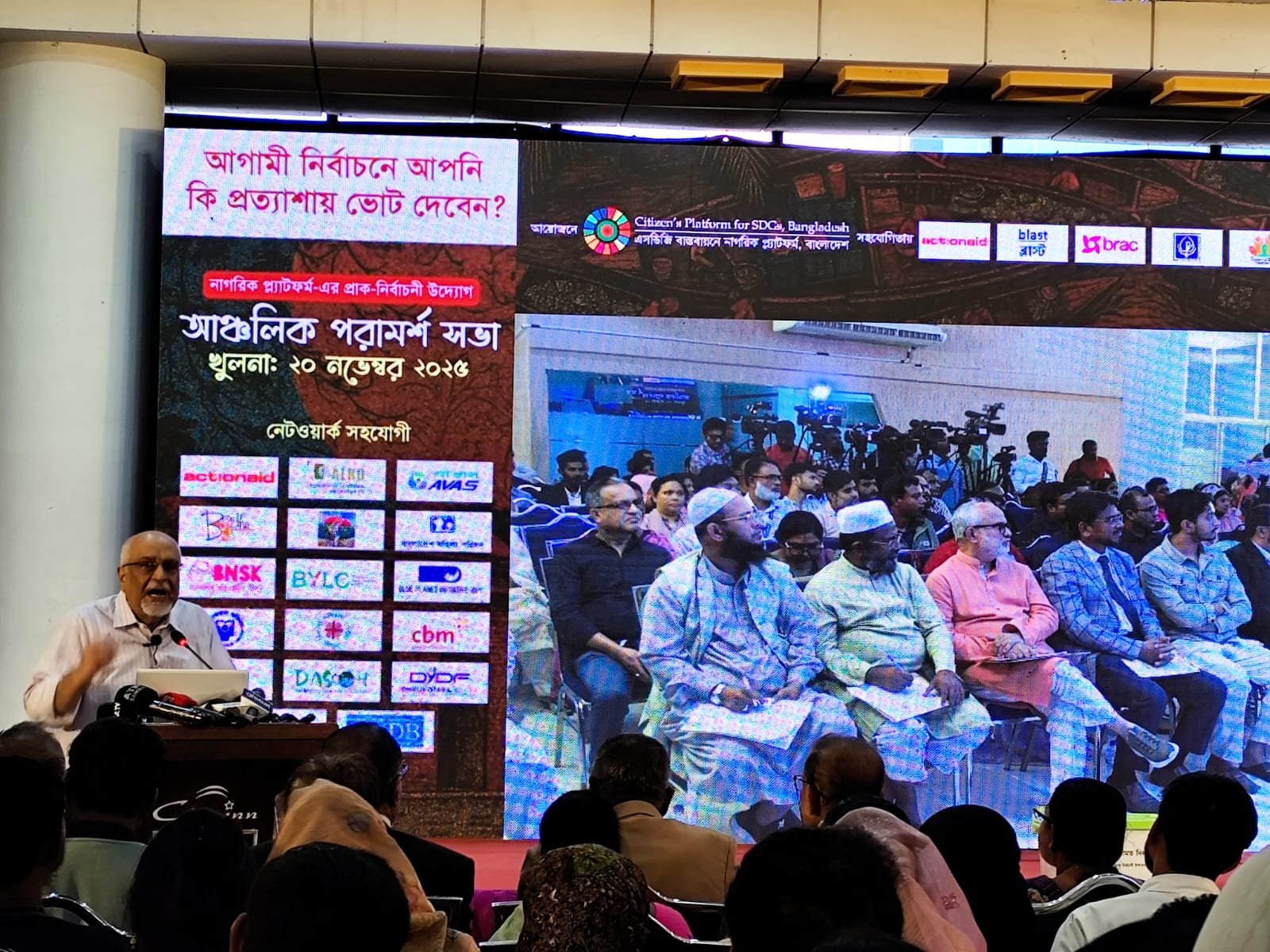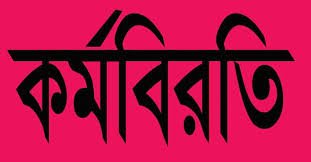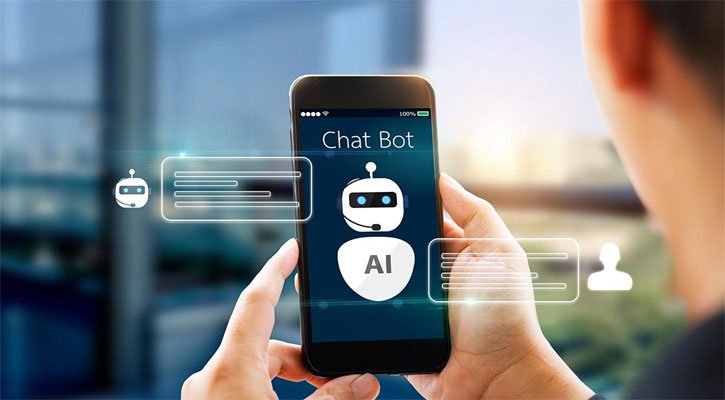তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক || ভয়েজ অফ জাস্টিস

ডিজিটাল যুগে ছবি ও ভিডিওর ক্ষেত্রে এআই ও ডিপফেইক প্রযুক্তি নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। প্রতিদিনই সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন ছবি ছড়িয়ে পড়ে, যা আসল নাকি কৃত্রিম তা শনাক্ত করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।
কিন্তু কিছু সহজ কৌশল জানা থাকলে ভুয়া কনটেন্ট চেনা সম্ভব।
ছবিকে জুম করুন
ছবি বড় করে দেখলে অস্বাভাবিকতা সহজে চোখে পড়ে। চোখ, ঠোঁট, চোয়াল, হাত বা আঙুলে ত্রুটি থাকতে পারে। মুখের চারপাশ ঝাপসা বা ভিডিওতে ঠোঁটের নড়াচড়া ও শব্দের মিল না থাকার ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। মুখ নড়াচড়া করলে দাঁতের অসঙ্গতি সহজেই বোঝা যায়।
আবেগ ও অনুভূতির সামঞ্জস্য দেখুন
স্বাভাবিক হাসি, কান্না বা উচ্ছ্বাস শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রভাব ফেলে। কিন্তু ডিপফেইক সফটওয়্যার এগুলো পুরোপুরি প্রতিফলিত করতে পারে না। ফলে আবেগ প্রকাশে অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ে।
পুরো দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করুন
একক ছবি অনেক সময় বাস্তব মনে হলেও গ্রুপ ছবি বা জটিল দৃশ্যে এআই ভুল ধরাতে পারে। হাত-পায়ের সংখ্যা, অদ্ভুত ভঙ্গি বা অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা লক্ষ্য করা যায়।
ব্যাকগ্রাউন্ড খতিয়ে দেখুন
ছবির বিষয়বস্তু ও পটভূমি যদি মানানসই না হয়, তবে সেটি সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে। এআই-তৈরি ছবিতে প্রায়ই এমন পটভূমি থাকে যার বাস্তব অস্তিত্ব নেই।
ছবির উৎস যাচাই করুন
ছবিটি কোথা থেকে এসেছে বা কেন তোলা হয়েছে তা দেখা জরুরি। রিভার্স ইমেজ সার্চ ব্যবহার করে সত্যতা যাচাই সম্ভব। জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের ছবি হলে বিষয়টি আরও সহজে যাচাই করা যায়।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এআইয়ের ছবি যতই নিখুঁত হোক না কেন, সতর্ক চোখ অসঙ্গতি সহজে ধরতে পারে। তাই ছবি দেখেই সিদ্ধান্ত না নিয়ে সবসময় খতিয়ে দেখা উচিত।